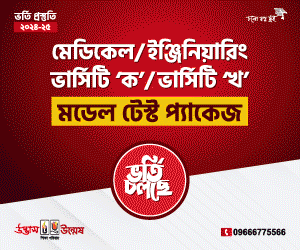আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার আগে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে স্বাধীনতার কঠিন অভিযাত্রায় সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে (পাকিস্তানি) সেনাবাহিনীর দখলকারীদের মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।’ এই ঘোষণার শুরুতেই উচ্চারণ করেছিলেন চূড়ান্ত ভাষ্যটি, ‘আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন’।
আমরা বাঙালিরা সেদিনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম দখলদার পাক হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। তার আগে পঁচিশে মার্চ রাতেই হানাদার জান্তারা গণহত্যা চালায় দেশ জুড়ে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি রুখে দিয়েছিলো হানাদার বাহিনীকে। অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সেনাটিকেও বাধ্য করেছিলো বাংলার মুক্তিবাহিনী আত্মসমর্পণে নত হতে। সহায়তা পেয়েছিলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর। দু’দেশের সেনা ও মুক্তিবাহিনী মিলে গড়ে উঠেছিল মিত্রবাহিনী। যৌথ এ বাহিনী সম্মিলিতভাবে শেষ আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করেছিলো নাফরমান ও নরঘাতক হানাদার পাকিস্তানি সেনাদের। হানাদারদের সহযোগিতায় বাঙালি নামধারী যে সব পদলেহীরা এগিয়ে গিয়েছিলো, পুরো নয় মাস তারাও এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান শুধু নেয়নি, হত্যা-খুন-ধর্ষণ-লুট ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের কাজও করেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন বাহিনী। সশস্ত্র সংগঠনও। শান্তি কমিটি, আলবদর, আল শামস, মুজাহিদ বাহিনী এবং রাজাকারের নামে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, কেএসপি, মুসলীম লীগের দুটি গ্রুপসহ ইসলামপন্থী নামধারী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। প্রত্যন্ত গ্রামেও তারা পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি হানাদারদের।
বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি-ঘরে লুট, অগ্নিসংযোগ শুধু নয়, লাইন করে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর-শিশুকে। পাশবিক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নারীদের। ধর্ষণের মাত্রা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো। হিটলারের ইহুদি জাতি নিধনের মতো এরা বাঙালি হত্যার নারকীয় তাণ্ডবে মেতেছিলো এই বলে যে, ‘তারা এদেশের মানুষ চায় না, চায় মাটি’। তাই গ্রহণ করেছিলো পোড়ামাটি নীতি। মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ মরণ কামড় খাওয়ার আগে এই নরঘাতক দল দেশের সেরা সন্তান চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিকদের বাড়ি থেকে ধরে চোখ বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন শেষে রায়ের বাজার ও মিরপুরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বেয়নেটে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। নয় মাসের প্রতিটি ঘটনাই ছিলো লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক, মর্মঘাতী।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দৃশ্য আজো ভাসে পেছনে তাকালে। যুদ্ধের তেপান্ন বছরের মাথায় সেই ভয়াবহতার দৃশ্য বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজকের প্রজন্মও এই বর্বরদের ক্ষমা করেনি, করতে পারে না। তারাও মনে করে ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মদান আর তিন লাখের বেশি মা-বোনের সম্ভ্রম হারিয়ে অর্জিত দেশে পরাজিত শক্তির অপতৎপরতা বন্ধ করা জরুরি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি জাতি চিহ্নিত করতে পেরেছিলো কে তার শত্রু, কে তার মিত্র। কিন্তু সেই শত্রুকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।
পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমিও ছিলাম। নবম শ্রেণির স্কুল ছাত্রটির চোখে মুখে তখন স্বাধীনতার স্পৃহা আর হানাদার বিতাড়ন দৃঢ় হয়ে উঠেছিলো। মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষুধা আমাকে করতে পারেনি দমিত। বিচলিত করতে পারেনি রক্তগঙ্গা। হত্যাযজ্ঞ আতঙ্কিত করেনি, করেনি ধংসযজ্ঞ। মর্টার, কামানের গোলা পারেনি আমাকে ধ্বংস করতে। বরং ওইসব শব্দ ছিলো আমার নিত্যসঙ্গী। প্রতি মুহূর্তে আমার আশপাশে মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দেখেছি। এই মাটি, আমার চোখের সামনে শহীদের রক্তপ্রবাহে দ্বিমাত্রিক হয়ে গেছে। আবার সেই রক্তবিন্দু থেকেই বিদ্রোহী ও অগ্নিশিখার আবির্ভাব দেখেছি। বাঙালির বিদ্রোহ, ওই অগ্নিমূর্তি, এই স্পর্ধা, এই অস্ত্র, এই রক্তের মধ্যেই আমরা প্রতিফলিত হয়েছি। তারপর একদিন আমাদের রক্তপ্রবাহ স্থবির হয়ে দাঁড়ায়। পর্বতের মতো বলীয়ান ও শক্তিধর এক পুরুষের জন্ম হয়-সেই আমার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার বৈভবে, তার আকুতি আর ক্রন্দনে, লাখো মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান হয়। স্বাধীনতা সেই স্পর্শ, সেই গৌরব অচঞ্চল মূর্তির মতো স্থানুবৎ দাঁড় করিয়ে রাখে।
রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘স্বাধীনতা বাইরের বস্তু নহে। মনের ও আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে যে গ্রহণ করিতে শিখিয়েছে এবং অপরের প্রতি উহা সম্প্রসারিত করিতে যে কুণ্ঠিত নয়, সেই প্রকৃত স্বাধীনতার উপাসক। স্বাধীনতা সম্বন্ধে অপরের প্রতি যাহার একান্ত অবিশ্বাস এবং সন্দেহ, স্বাধীনতার ওপর তাহার কিছুমাত্র নৈতিক দাবি থাকে না, সে পরাধীনই রহিয়া যায়। আমি তাই আমার দেশবাসীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, স্বাধীনতার ওপর তাহাদের আকাঙ্ক্ষা তাহা কি বাইরের কোনো বস্তু বা অবস্থা বিশেষের ওপর নির্ভরশীল? তাহারা কি তাহাদের সমাজের ক্ষেত্রে শত রকমের অন্যায় ও অসঙ্গত বাধা হইতে বিমুক্ত এতোটুকু স্থান ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন, যাহার ভিতর তাহাদের সন্তান-সন্ততি মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদায় দিন দিন বড় হইয়া উঠিতে পারে?’ রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার মূল্য' প্রবন্ধে মানবতাবোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। একাত্তর সালে মানবিকতার জয় হয়েছিলো। আর পরাজয় ঘটেছিলো দানবিকতার।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ দৃশ্যত একাত্তরের মার্চ থেকে শুরু হলেও এর প্রেক্ষাপট অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো। এটি ছিলো দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এবং নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তরের ২৫-২৬ মার্চ রাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে আটক হবার নেপথ্যে একটা রাজনৈতিক, কৌশলগত কারণ অবশ্যই ছিলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি শুধু নয়, ১৪ কোটি পাকিস্তানিদেরও তিনি নির্বাচিত অবিসংবাদিত নেতা। যার অঙ্গুলি হেলনে ও নির্দেশে তখন বাংলাদেশ চলছিলো। তিনি পালিয়ে বা আত্মগোপন করলে তো হানাদার পাকিস্তানি ও তার মিত্ররা সুযোগ পায় বিশ্বমানবতাকে তাদের পক্ষে নেয়ার। এমনিতেই তখনকার বৃহৎ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা শুধু নয়, অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে পাকিস্তানকে বলীয়ান করছিলো। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমতের সমর্থন লাভ করা সহজতর হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধেও সময় যদিও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। বন্দি মুজিব হয়ে উঠেন দ্বিগুণ শক্তিশালী। তার নাএেন পরিচালিত হয় যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগকে এককভাবে দায়ী করে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলো। ‘পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ’ সৃষ্টির পথ সুগম করার অভিযোগ এনে ইয়াহিয়া খানরা বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে বদ্ধপরিকর ছিলো। কিন্তু ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিশ্বজনমতের চাপে ও ভয়ে সেই দণ্ড কার্যকর করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হবার পর পরই বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলো। ‘বাংলাদেশ এক ঘোষণায় স্বাধীন হয়ে গেছে’ বলে যারা ভাবেন ও বলেন, তারা আসলে এদেশকেই মেনে নিতে পারেন না বা ইতিহাসের বিরুদ্ধে, পরাজিত শক্তির পক্ষাবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে তার জাতিকে স্বাধীনতার জন্য তৈরি করেছিলেন। জাগিয়ে তুলেছিলেন জাতীয়তাবাদী সত্তা। জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো তার অনন্য কৃতিত্ব। আর এই প্রক্রিয়াতো একদিনে বা হঠাৎ করে শুরু হয়নি। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিলো। উনসত্তর সালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে ‘বাংলাদেশ’ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এদেশের রাজনীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় প্রবাহিত করার পেছনেও বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিলো অনন্য। বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছার ধারক বঙ্গবন্ধু বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড একটি স্বাধীন পতাকা এনে দিয়েছেন।
যে জাতিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছেন, যে জাতিকে বিশ্বাস করতেন গভীরভাবে, ভালবাসতেন, সুখ দুঃখের কথা অনুধাবন করতে পারতেন, সেই বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন পাকিস্তানি ভাবাদর্শে লালিত বিপথগামী বাঙালি সেনাদের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে পাকিস্তানি ভাবধারার প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়, তাদের হাতেই উত্থান ঘটে একাত্তরের পরাজিত শক্তির এবং সাম্প্রদায়িকতার। গর্ত থেকে, পলাতক জীবন থেকে একে একে সব বেরিয়ে আসে। তাদের তৎপরতা ছিলো এমন যে, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার- এর ব্রতে তারা বলীয়ান। পাকিস্তান আমলের মতোই ধর্মরক্ষার লেবাসে তারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সুফলগুলো একে একে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কামিয়াব হয়। প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে আবহমান ‘আমরা বাংলার উত্তরাধিকার, বাঙালিত্বের সেক্যুলার সত্ত্বা এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্লীন মৌল সতাকে।
সর্বোপরি এদেরই শকুনি আঁচড়ে বিকৃত, খণ্ডিত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত অন্যতম স্বর্ণকমল পবিত্র সংবিধান। বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির ওপর পঁচাত্তর পরবর্তী যে আক্রমণ, তাতে এই ফিরে আসা ও আবির্ভূত ঘাতকদের ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ শুধু নয়, একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কাজটি ও চালানো হচ্ছে অদ্যাবধি। দেশকে পাকিস্তানি কায়দায় পশ্চাদপদ করার জন্য সর্বত্র ধর্মের জিগির তোলা হয়। ক্রমশ তা সমাজের নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে।
বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির কেনো স্বাধীনতা প্রয়োজন, কেনো দেশ ভাগের ২৪ বছর পরও বাঙালি স্বাধিকারহীন, কী তার লক্ষ্য, অভিযাত্রা-সবই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে তুলে ধরেছিলেন। বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুরা থেমে ছিলো না। পদে পদে বিড়ম্বনা তৈরি করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে আরো বিপর্যস্ত করার জন্য নানামুখী তৎপরতা চালিয়েছে। অবস্থা থেকে উত্তরণে বঙ্গবন্ধু সার্বক্ষণিক সচেষ্ট ছিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার পরই তাকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের ১৯৫ জন কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সেনা ও সরকারি কর্মকর্তা রেসকোর্স ময়দানে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিলো। অপরদিকে, পাকিস্তানে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনার কাজটিও গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। তাদের পরিবারের সদস্যরা বঙ্গবন্ধু সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগে অনশন কর্মসূচিও নেয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী এ দেশীয় দোসরদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই পর্যন্ত আটটি আদেশের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিলো। বিচার কার্যক্রমও চলছিলো। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালস আদেশে তিনটি সংশোধনী আনা হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ত্রিশে নবেম্বর পর্যন্ত সারা দেশ থেকে এ আইনের অধীনে ৩৭ হাজার ৪৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিলো। দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছিলো তার মধ্যে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিলো। অভিযুক্তদের মধ্যে ৭৫২ জন দোষী প্রমাণিত হয়েছিলো। ২ হাজার ৯৬ জন ছাড়া পায়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নবেম্বর দালাল আইনে আটক যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মেলেনি তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিলো।
তখন দেশের পরিস্থিতি এমন যে, বাংলাদেশকে ঘিরে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তান, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান থেকে তখনো সরে আসেনি। আর দেশের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরা আঁটঘাট বেঁধে দেশ ও সরকারবিরোধী তৎপরতা চালায়। পরস্পরবিরোধী দাবিতে রাজপথ মুখরিত করে তোলে। কেউ চায় পাকিস্তানি সেনাদের বিচার। কেউ চায় পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। কেউ চায় ঘাতক দালালের বিচার। আবার দালাল আইন প্রত্যাহার না করলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে হুমকি দিয়ে অনশনে নেমেছিলেন স্বয়ং মওলানা ভাসানী। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে দালাল আইন বাতিলের জন্য ভাসানী ন্যাপ, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ, সর্বোপরি নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এই দলগুলোর ছত্রছায়ায় তখন স্বাধীনতাবিরোধীরা আশ্রয় নিয়েছিলো। স্বচক্ষে দেখা, তারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ও মিছিলো করত। ভাসানীর প্রাচ্যবার্তা, হক কথা, অলি আহাদের ইত্তেহাদ, চীনপন্থীদের নয়াযুগ এবং গণকণ্ঠ নামে জাসদ সমর্থিত সংবাদপত্রগুলো দালালদের পক্ষাবলম্বন করে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলা, বাংলাস্তান করার দাবিও তোলে। বামপন্থী বদরউদ্দিন উমরের পিতা ইতিহাসখ্যাত আবুল হাশিমও মুসলিম বাংলার পক্ষে কলম ধরেন। অবশ্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে তাদের পক্ষাবলম্বনে বাধ্য করেছিলেন। ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পদক মশিউর রহমান যাদুমিয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে দালাল আইনে গ্রেফতার হন এবং জেলে আটক থাকাবস্থায় বিচারে সাজাপ্রাপ্ত হন। মুসলিম লীগ, পিডিপি ইত্যাদি দলের আটক ব্যক্তিদের পরিবার ও সহকর্মীরা জাসদের পতাকার নিচে আশ্রয় নিয়ে দালাল আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা দালাল আইন বাতিল ও আটকদের মুক্তির দাবিতে তোপখানা রোডে সমাবেশ করতো। এই দাবিতে সমাবেশ জেলা ও থানা পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এসব সমাবেশ থেকে অভিযোগ তোলা হতো এখনকার মতোই যে, এই আইনের মাধ্যমে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করছে। নিরীহ লোককে দালাল সাজিয়ে সাজা দেয়া হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা চালানো হয়। এদের চাপেই সম্ভবত সরকার সাধারণ ক্ষমার পদক্ষেপ নেয়। তবে সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোটে বলা হয়েছিলো, ‘ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা যানবাহনে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না’। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও দালাল আইনে আটক ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এসব অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিলো এবং তাদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো।
অপরদিকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা শুরু হয় আটকেপড়া বাঙালিদের। যুদ্ধাপরাধী ও পাকি হানাদারদের স্বদেশে ফেরার বিনিময়ে প্রত্যাগত হন তারা। তবে পাকিস্তানি সেনাদের ফেরত নেবার সময় সিমলা চুক্তিতে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার অঙ্গীকার দিয়েছিলো পাকিস্তান। কিন্তু তারা তা করেনি। বঙ্গবন্ধুর সরকার পাকিস্তান ফেরত প্রায় সকল সেনা অফিসারকে পুনর্বহাল করে। এজন্য ‘স্ক্রিনিং বোর্ড করা হয়। বোর্ডের সদস্যদের কাছে এরা কেউ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধঃস্তন বা সহকর্মী ছিলেন। তাই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য যাদের মজ্জাগত, তেমন সামরিক-বেসামরিক আমলারাও পুনর্বাসিত হলো। যাদের বাদ দেয়া হয়েছিলো, তাদের পরিবারগুলোর পক্ষ থেকেও সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিলো। বোর্ড সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ‘অফ’ রেখেই ঢালাও নিয়োগ দেয়ায় সমস্যা বাড়ে। মুক্তিযোদ্ধা বনাম পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে পদ-পদবীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তীব্র ও প্রকট হয়ে ওঠে। সেসব অবশ্য ইতিহাসের অংশ।
১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধের ইতিহাস উল্টে যায়। ক্ষমতায় দখল করার পর সামরিক জান্তারা প্রথমেই দালাল আইন বাতিল করে। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর আইনটি বাতিলের মাধ্যমে স্বদেশি যুদ্ধাপরাধীর বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে এই ঘোষণার পর যারা এই আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করেছিলো সেই ভাসানী ন্যাপ, জাতীয় লীগ, গোপন বামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ এমনকি পলাতক মুসলিম লীগসহ অন্যান্য ইসলামপন্থী দলগুলো ক্ষমতা দখলকারীর পেছনে জড়ো হলো। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসে।
১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের যে জাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, সেই দেশটি আবার পরাধীনতায় শুধু নয়, একাত্তরের ঘাতক দালালদের কজায় চলে যায়। বাঙালির সব ইতিহাস, ঐতিহ্য ক্রমশ বিকৃত ও বিলীন হতে থাকে। যে মুক্তিযুদ্ধ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলো এবং ওরা পালিয়ে গিয়েছিলো, সেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরায় স্বীকৃতি শুধু নয়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত করা হতে থাকে, একাত্তরে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ভূমিকা পালনকারী জামায়াতে ইসলামী। স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে না পেরে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ নামে মাঠে নামে। শুধু তাই নয়, এই দলটিকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের সাজানো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১টি আসন দেয়া হয়। স্বাধীনতাবিরোধী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, পিডিপির চিহ্নিতরা সংসদে আসন পায়। আর এভাবে তারা ৩০ লাখ বাঙালি ও ৩ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফেরানোর জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনতার শত্রুরা রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সমাজের বিভিন্ন স্থানে দ্রুত অবস্থান নেয়। শাসকরা তাদের পুনর্বাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে।
সবচেয়ে বড় আঘাতটা এই সময়ে হানা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর। লোভ, মোহ, লালসা, ক্ষমতার লোভ এমন পর্যায়ে যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারাও ভুলে যায় স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে জিম্মি তারা। বরং মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবার ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র একাকার হবার এই কলঙ্কজনক সময়গুলোতে জনগণ বিস্মিত হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু জনগণের ব্যাপক অংশ এদের মেনে নিতে পারেনি। যারা একাত্তর খ্রিষ্টাব্দে এদের নৃশংসতা ও নির্মমতার শিকার এবং প্রত্যক্ষদর্শী তারা কোনভাবে ক্ষমা করেনি, করতে পারেনি। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষোভগুলো গত চার দশকের বেশি সময় ধরে সঞ্চিত হতে হতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চে বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে।
তাই দেখা যায়, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষেও দেশের তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে একাত্তরের চেতনাকে সমুন্নত রেখে বেঁচে থাকার প্রাণপণ লড়াই করছে। এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া নয়, এ যে দীর্ঘ ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলীন হতে থাকার মুহূর্তে এসে ঘুরে দাঁড়ানো। সেই লড়াই খুব সহজতর নয়। কিন্তু তা অব্যাহত থাকবে এই কারণে যে, এ দেশের মানুষ অসীম ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন স্বদেশ পেয়েছিলো। যার শিখরে ছিলেন তাদেরই আরাধ্য পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি এনে দিয়েছেন তাদের একটি ভূ-খণ্ড, কটি রাষ্ট্র, একটি স্বাধীন জাতির পরিচয়। সে সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া সহজ সাধ্য নয়। তা পাকিস্তানিরা বুঝেছিল। শুধু বুঝতে চায় না একাত্তরের নরঘাতকরা। ওরাই স্বাধীনতার বড় শত্রু। মুক্তির ব্রতে বাঙালি জাতি সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিলো। আজ ৫৩ বছর পাড়ি দিতে দিতে মূল্যায়ন জাগে ‘বাংলাদেশ পরাভূত হতে জানে না’।
লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)