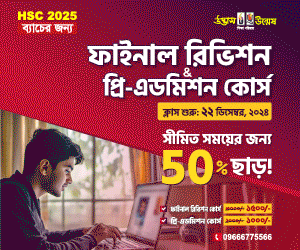শতবছর আগের আর আজকের ঈদ-উল আজহার মধ্যে একটা বড় তফাৎ রয়েছে। বিশেষ করে তখন ঈদ-উল আজহাকে বলা হতো 'বক্রা ঈদ, বকরিদ বা বকরি ঈদ'। এর বানান বিভিন্ন হলেও ভাব ছিল অভিন্ন—যে ঈদে বকরি কোরবানি করা হয়। প্রশ্ন হলো, বকরি কেন? কেন নয় গরু? উত্তরটা মিলবে আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনী থেকে: 'বক্রা ঈদে গরু কোরবানি কেউ করিত না। কারণ জমিদারের তরফ হইতে উহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খাশি-বকরি কোরবানি করা চলিত। লোকেরা করিতও তা প্রচুর।' 'জমিদারের তরফ হইতে উহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল' বিধায় বাংলার মুসলমানরা সাধারণত বকরি কোরবানি করতো। যে কারণে ঈদের নামই হয়ে গিয়েছিল বকরি ঈদ।
কতজন মুসলমানের কোরবানির সামর্থ্য ছিল? তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে সহজেই অনুমেয় যে, সমাজের হাতেগোনা কিছু মুসলিম পরিবারের পক্ষেই সম্ভব ছিল কোরবানি করা। যে কারণে আমরা দেখি, শতবর্ষী মুসলমান ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনীতে ঈদুল ফিতর বা মোহররম নিয়ে যেমন চিত্র উঠে এসেছে, কোরবানির ঈদ নিয়ে তেমনটা আসেনি। তবে, ব্রিটিশ আমলের শেষদিকের কিছু চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্নজনের আত্মজীবনীতে।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন: 'বকরিদে আমরা প্রতিবছর কুরবানি দিতাম না—মাঝে মাঝে তা বাদ পড়তো—ভক্তির অভাবে অতোটা নয়, যতোটা সামর্থ্যের অভাবে। বড়োরা চেষ্টা করতেন পশু জবাই থেকে আমাদের আড়াল করতে। আমরা ছোটোরা ততোধিক উৎসাহ ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে জবাই দেখে ফেলতাম। দেখার পরে কিন্তু অনেকক্ষণ বিষাদে মন ছেয়ে যেতো। তবে শেষ পর্যন্ত এই বিষণ্নতা পেছনে ফেলে দেখা দিতো কুরবানির গোশত খাওয়ার উৎসাহ।'
দেখা যাচ্ছে আনিসুজ্জামানের পরিবার কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবার হওয়া সত্ত্বেও 'সামর্থ্যের অভাবে' কোরবানি 'মাঝে মাঝে বাদ পড়তো'। তাহলে অজপাড়াগাঁয়ের মুসলিম পরিবারগুলোর অবস্থা কেমন ছিল?
তবে, কোরবানি করার সামর্থ্য সবার না থাকলেও ঈদের নামাজ আদায় করতে কার্পণ্য করতেন না মুসলমানরা।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর রচিত ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'ঈদল আজহা' নামক গ্রন্থ। বইয়ের ভূমিকায় নবাব লিখেছেন, তার গ্রামের আশপাশে কোনো ঈদগাহ না থাকায় ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ধনবাড়ি গ্রামের একটি মাঠকে ঈদগাহ হিসেবে নির্ধারণ করেন। সে ঈদগাহে সর্বপ্রথম কোরবানির ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে জামাতের ইমামতি করেছিলেন নবাব সাহেব স্বয়ং। ইমামতি করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, কোরবানির ঈদ সম্পর্কে বাংলার মুসলমান নিতান্তই কম জানে। কারণ তাঁরা আরবি-ফারসি ভাষা তেমন জানে না। আর বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ের বই তখন ছিল দুর্লভ। এই ভাবনা থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কোরবানির ঈদ নিয়ে বিস্তারিত মাসয়ালা ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে রচনা করেছেন 'ঈদল আজহা'। এখন আমরা চল্লিশের দশকে বেড়ে ওঠা দু'জনের স্মৃতিকথার মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে কেমন আয়োজন হতো সে বিষয়ে জানবো।
চট্টগ্রামের পটিয়ায় জন্মগ্রহণ করা দৌলতুল আলম জানাচ্ছেন কোরবানি উপলক্ষে তাদের পারিবারিক রেওয়াজের কথা: 'প্রতি বৎসর কুরবানীর সময় আমাদের পরিবারে মা, বাবা আমরা প্রায় দেড় ডজন ভাই-বোন ছাড়াও আত্মীয়, অনাত্মীয় এবং কাজের লোকের সমাবেশে বাড়িটি উৎসবমুখর হয়ে উঠত। তাই গরু-ছাগল মিলিয়ে কুরবানী হতো বিরাট আকারের। বাবাকে নিজের হাতে গরু জবাই করতে দেখেছি। একবার কুরবানীর সময় জবাইকৃত গরু অর্ধেক শোয়া অবস্থায় মাথা তুলে দু'দিকে এমন জোরে আছড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এখনই উঠে দৌড় লাগাবে। আমরা ছোটরা সেই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য বধ্যভূমিতে ছুটে যেতাম।'
এ থেকে ২টি বিষয় স্পষ্ট: ১. কোরবানিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক মিলনমেলা সৃষ্টি হতো, ২. ছোটদের জন্য গরু কোরবানির পূর্বাপর দৃশ্য ছিল চমকপ্রদ।
জাহানারা ইমামেরা বেড়ে ওঠেন পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের খানদানি পরিবারগুলোতে কোরবানিকে কেন্দ্র করে কেমন আয়োজন হতো, বিস্তারিত এসেছে তার স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন: 'কোরবানীর সময় আমাদের বাড়িতে চালের আটার রুটি বানানো হত—সে একটা দেখবার মত জিনিস। রসুনের খোসার মত পাতলা রুটি, ধবধবে সাদা এবং সুগোল। বাড়ির মেয়েরা আগের রাতে বারোটা একটার সময় দহলিজের সামনের সেই যে কাজীপুকুর—সেই পুকুরটায় গোসল করে আসতেন৷ কাজী পুকুরের সানবাঁধানো ঘাট ছিল, চারকোনা পুকুরটির পাড়গুলি উঁচু ছিল, পানি ছিল পরিষ্কার টলটলে। রাত দুপুরে পর্দার হানি হবে না বলেই বোধ হয় দাদাজানের অমত ছিল না বাড়ির বউঝিদের পুকুরে গোসল করতে যেতে দিতে। গোসল করে বাড়িতে এসে নতুন শাড়ি পড়ে বউ-বিবিরা ওজু করে বিসমিল্লা বলে কোরবানীর রুটি বানাতে বসতেন। আগের দিনই ঢেঁকিতে আটা কোটানো হয়েছে। রুটি বানানো হত দু'শো তিনশো!
বাঁশের পাতলা চটা দিয়ে তৈরি প্রায় একহাত উঁচু খুঁচি (গ্রামীণ ব্রেড-বকস) চারপাঁচটা আগের দিন ধুয়ে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়েছে—সেগুলিতে রুটি সেঁকে ফেলা হচ্ছে, রুটি যাতে গরম থাকে তার জন্য পুরনো শাড়িছেঁড়া কাপড় চারভাঁজ করে খুঁচির মুখে ঢাকা দেওয়া। এই কাপড়ও আগের দিন খুব ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখা হয়েছে।
এত বেশী রুটি বানানোর কারণ হল শুধু বাড়ির আত্মীয়-স্বজন নয়, পাড়া প্রতিবেশী, অন্য পাড়ার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং গ্রামের অভাবী লোকজন সবাইকেই রুটি হালুয়া গোশত দিতে হবে। বাড়িতেও ক'দিন ধরে কেবল রুটি-গোশতই খাওয়া হবে। যত মেহমান আসবেন, সবাইকেই রুটি-হালুয়া-গোশত খাওয়াতে হবে। সে যুগে ঈদ-বকরিদের মেহমানরা একালের মেহমানদের মত নাক সিঁটকে এক চামচ সেমাই বা একটা রুটির কোনা ছিঁড়ে খেতেন না, তাঁরা বেশ ভালো করেই পেট ভরে খেতেন। খেতে পারতেনও তাঁরা সেকালে। তাই যাঁরা খাওয়াতেন, তাদের আয়োজনটাও এ রকম বিরাটই করতে হত।
বকরিদের সকালে কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু মুখে দিতেন না। পুরুষরা গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে নামাজ পড়তে যেতেন খালি পেটেই। ফিরে এসে একেবারে কোরবানী দিয়ে তারপর বাড়িতে ঢুকতেন। ততক্ষণে মেয়েদের রুটি, হালুয়া, সেমাই, ফিরনী—সব রান্না শেষ।
... যেখানে দহ্লিজ ঘরের পাশে আমাদের গোয়াল-বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটু আগেই কোরবানী দেওয়া হয়েছে। ততক্ষণে দু'একটা গরু-ছাগলের চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেছে, আমাদের লক্ষ্য গরুর কলজে। আমরা প্রত্যেকেই একটা করে বাটি হাতে নিয়ে এসেছি—গরুর পেট থেকে কলজে বেরোনো মাত্র একটা বা দুটো কলজে সর্বাগ্রে ছোট ছোট করে কেটে আমাদেরকে দেয়া হবে—আমরা ওগুলো নিয়ে আবার বাড়ির ভেতরে ছুটব, সেখানে নানী, ফুপু ও চাচীরা কলজেগুলো শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসে দেবেন আমাদের।
সব গরু ছাড়িয়ে কেটে ভাগ করতে প্রচুর সময় লেগে যেত, সেজন্য প্রথমেই কিছুটা গোশত কেটে দাঁড়িয়ে পাল্লায় ওজন করে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দেয়া হত তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য—যাতে দুপুরেই কিছুটা খেতে পারা যায়। ওই গোশতটারও হিসেব রাখা হত, সাতভাগ করার সময় ব্যালান্স করে দেবার জন্য।
ঝলসানো কলজে দিয়ে যে মহাভোজের সূচনা হত, তা শেষ হত কোর্মা, রেজালা, কোপ্তা, কাবাব, দো-পেঁয়াজা, ঝাল-কারী দিয়ে, সঙ্গে থাকত কখনো পোলাও, কখনো পরটা এবং সদাসর্বদা সেই চালের আটার বেলা রুটি। বেলুনে বেলে বানানো হয় বলে যার নাম বেলারুটি (উচ্চারণ-ব্যালা)। এই ভোজ চলত দু'তিন দিন ধরে।
তারপরেও ভুনা গোশত খাওয়ার জের চলত ১০-১৫দিন। সেকালে ত' ফ্রিজ ছিল না। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বউ-বিবিদের মস্তবড় কাজই ছিল বিরাট বিরাট ডেকচি-কড়াইতে রাখা গোশত ভাল করে জ্বাল দেওয়া। এটা বড়ই খাটনির কাজ ছিল, বিরক্তিকর তো বটেই। জ্বাল দেওয়ার দোষে অনেক সময় গোশত নষ্ট হয়ে যেত। সে জন্য খুব দায়িত্বশীল এবং জাঁহাবাজ ধরনের একজন মুরুব্বি এসবের তদারকিতে থাকতেন। কোরবানীর গোশত মহরমের চাঁদে খাওয়া নাকি খুব পুণ্যের কাজ—তাই কিছুটা গোশত খুব যত্নসহকারে জ্বাল দিয়ে দিয়ে রাখা হত।'
তার এই স্মৃতিকথাতেও কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। ১. কোরবানির ঈদ উপলক্ষে পরিবারের সব সদস্যের মিলনমেলা সৃষ্টি। ২. গরুর গোশত দিয়ে খাওয়ার জন্য আগের রাত থেকেই রুটি বানানোর কাজে লেগে যাওয়া এবং রুটি গরম রাখার জন্য শাড়ি দিয়ে অদ্ভুত নিয়ম আবিষ্কার করা। ৩. বর্তমান সময়ে আমরা যেভাবে অন্যের বাড়িতে গিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে জড়তায় ভুগি, সেকালে তেমনটি ছিল না। মেজবান ও মেহমান দুপক্ষেরই ছিল দিলখোলা সম্পর্ক। ৪. গোশতের ভাগে যেন ভুলেও কম-বেশি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা।
এটা খুব স্বাভাবিক যে, শতবর্ষ পূর্বের কোরবানির ঈদ উদযাপনের ধরন হুবহু একই থাকবে না, শতবর্ষ পরে কিন্তু রেশ তো রয়ে যায়! আগের মতো এখনো রাজধানী ফাঁকা হয়ে যায় ঈদের ২ দিন আগেই। সারাবছর যে যেখানেই থাকুক না কেন, একসঙ্গে কোরবানি দেওয়ার খেয়ালে সবাই ফিরে গ্রামে। মা-বোনদের তৈরি রুটিতে এখনো লেগে আছে মাংসের ঝোল। কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে পারিবারিক যে মিলনমেলা এবং পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত খাবার আয়োজন, তার মাধ্যমেই যেন সেকালের ঈদের সঙ্গে একালের ঈদের সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। (নাঈম আহসানের লেখা, ঈষৎ সংক্ষেপিত)